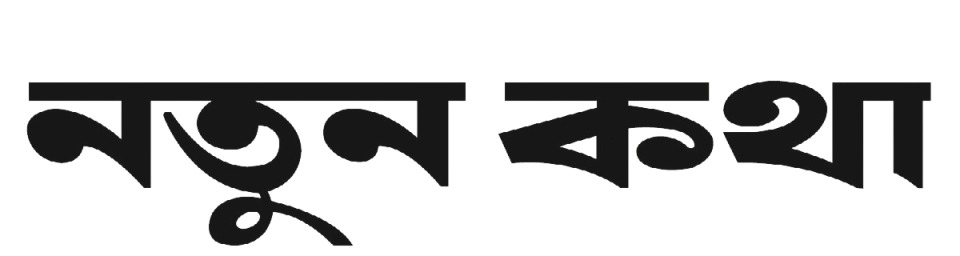স্লাভো জিজেকের (Slavoj Žižek) মতে, পোস্ট-আইডিওলজি কোনো মতাদর্শের অনুপস্থিতি নয়, বরং এটিই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী, চতুর এবং কার্যকর মতাদর্শ। কেন? কারণ এটি নিজেকে মতাদর্শ হিসেবে পরিচয় দেয় না।
জিজেকের ভাষায়, আজকের দিনের শাসক মতাদর্শ (Ruling Ideology) আমাদের বলে না যে, “এই নির্দিষ্ট মতাদর্শকে বিশ্বাস করো”। বরং সে বলে, “কোনো মতাদর্শেই বিশ্বাস করো না। বড় বড় কথায় কান দিও না। ওসব ‘ইজম’-এর দিন শেষ। শুধু বাস্তববাদী হও, জীবনকে উপভোগ করো, নিজের কাজ করো।” আর এটাই হলো তার সবচেয়ে বড় চালাকি। যখন আমরা মনে করি যে আমরা কোনো মতাদর্শ দ্বারা চালিত হচ্ছি না, আমরা মুক্তভাবে চিন্তা করছি, ঠিক তখনই আমরা সবচেয়ে গভীরভাবে শাসক মতাদর্শের জালে জড়িয়ে পড়ি (Žižek, 1994)। “আমি কোনো ইজমে বিশ্বাস করি না, আমি একজন বাস্তববাদী মানুষ” – এই কথাটিই হলো আজকের যুগের প্রধান মতাদর্শিক বক্তব্য।
এই শাসক মতাদর্শটি হলো বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ (Global Capitalism)। এটি নিজেকে কোনো ‘ইজম’ হিসেবে উপস্থাপন করে না, বরং ‘স্বাভাবিক’, ‘প্রাকৃতিক’ বা ‘একমাত্র সম্ভব’ অবস্থা হিসেবে আমাদের সামনে হাজির করে। আমরা ধরেই নিই, এর কোনো বিকল্প নেই – যেমনটা মার্গারেট থ্যাচার বলতেন, “There Is No Alternative” (TINA)।
জিজেক দেখান, আগেকার দিনে মতাদর্শ কাজ করত ‘মিথ্যা চেতনা’ (false consciousness) হিসেবে। মানুষ না জেনেই শোষণের ব্যবস্থাকে সত্য বলে মেনে নিত। কিন্তু আজকের পোস্টমডার্ন বা সিনিক্যাল (cynical) যুগে মানুষ সবকিছুই জানে। সে জানে যে কর্পোরেশনগুলো পরিবেশ ধ্বংস করছে, রাজনীতিবিদরা মিথ্যা কথা বলছে, ভোগবাদ আমাদের সুখী করতে পারছে না। কিন্তু সে তারপরেও সেই ব্যবস্থার অংশ হয়েই থাকে।
এই অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জিজেক ‘বিদ্রূপাত্মক কারণ’ বা সিনিক্যাল রিজন (Cynical Reason) ধারণাটির কথা বলেন। আজকের মানুষ বলে, “আমি জানি স্টারবাকস কফি চাষীদের শোষণ করে, কিন্তু তাদের কফিটা খেতে ভালো, আর আমি একা না খেলে কী-ই বা হবে?” অথবা, “আমি জানি রাজনীতি একটা নোংরা খেলা, কিন্তু আমার ভোট দিয়ে কী হবে?” এই যে “আমি জানি, কিন্তু তারপরেও…” (I know perfectly well, but still…) – এটাই হলো সিনিক্যাল দূরত্ব (Cynical Distance)। আমরা কোনো কিছুকেই আর মন থেকে বিশ্বাস করি না, কিন্তু ব্যবস্থার নিয়মগুলো ঠিকই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি (Žižek, 1989)।
কেন? কারণ মতাদর্শ এখন আর আমাদের বিশ্বাসে বা চেতনার গভীরে বাস করে না; এটি বাস করে আমাদের দৈনন্দিন কাজে, আমাদের ছোট ছোট অভ্যাসে, আমাদের অচেতন রিচুয়াল বা আচার-অনুষ্ঠানে। আমরা যখন দোকানে গিয়ে প্লাস্টিকের বোতলে ভরা জল কিনি, তখন হয়তো আমরা মনে মনে পরিবেশ দূষণের জন্য আফসোস করি, কিন্তু বোতলটা আমরা ঠিকই কিনি। জিজেকের মতে, আজকের মতাদর্শ আমাদের কাছ থেকে আন্তরিক বিশ্বাস দাবি করে না, সে শুধু চায় আমরা যেন নিয়মগুলো মেনে চলি, খেলাটা চালিয়ে যাই।
এই প্রেক্ষাপটে, পোস্ট-আইডিওলজি তত্ত্বটি হলো সেই সিনিক্যাল মানসিকতারই একটি তাত্ত্বিক রূপ। এটি আমাদের বলে, “বড় বড় আদর্শের কথা বলে আর কী হবে? এসব তো আর কাজ করে না। তার চেয়ে বরং সিস্টেমের ভেতরে থেকেই যতটা সম্ভব ভালো থাকার চেষ্টা করো।” এটি আমাদের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষাকে কেড়ে নেয় এবং আমাদের এক ধরনের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার দিকে ঠেলে দেয়।
জিজেকের কাছে, এই আপাত মতাদর্শহীনতার যুগ আসলে মতাদর্শের চূড়ান্ত বিজয়। কারণ পুঁজিবাদ এখন আর একটি বিকল্প হিসেবে উপস্থিত নয়, সে নিজেই হয়ে উঠেছে প্রকৃতির মতো স্বাভাবিক এবং অনিবার্য এক বাস্তবতা। আর এর থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো, এই অদৃশ্য মতাদর্শকে দৃশ্যমান করা এবং একটি র্যাডিক্যাল রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ‘স্বাভাবিক’ অবস্থাকে ভেঙে ফেলা।
লেখাটি- সংগৃহীত এবং মতামত লেখকের নিজস্ব।
লেখক- সুমিত রায়
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫