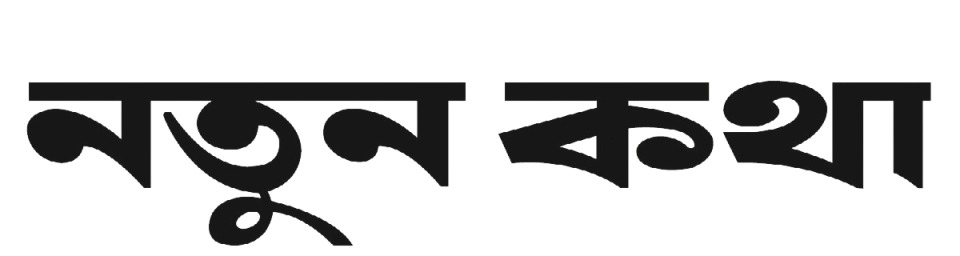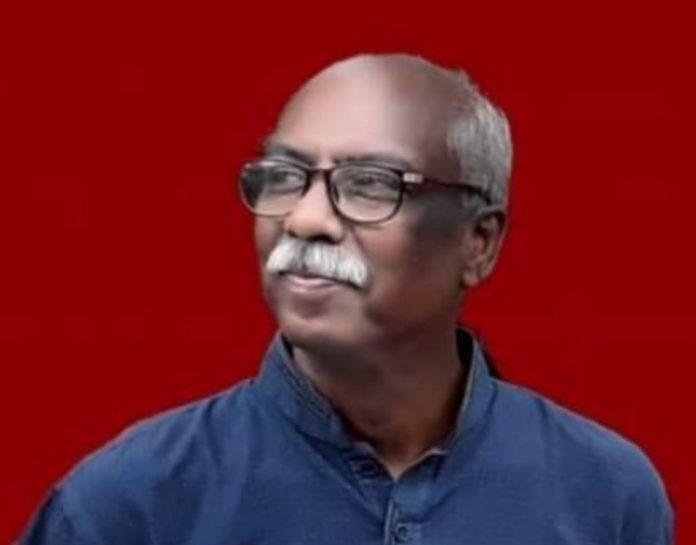বাংলাদেশ আজ কেবল একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নয়, বরং হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক একটি জাতিসত্তা, যা এক গভীর সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার সহস্রাব্দেরলোকায়ত, লোকজ সংস্কৃতি এখন চরম উগ্র ধর্মান্ধদের আঘাতের মুখে। নদীবিধৌত এই বদ্বীপেরজীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস ও লোকদর্শন এক স্বতন্ত্র ধারায় বিকশিত হয়েছে, যা কঠোর, আনুষ্ঠানিকধর্মীয় মতবাদ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামো, বিশেষতআন্তোনিও গ্রামসি (Antonio Gramsci)-এর সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ (Cultural Hegemony) এবং এডওয়ার্ড সাঈদ (Edward Said)-এর প্রাচ্যবাদ (Orientalism)-এর ধারণা-র মধ্য দিয়ে দেখলে স্পষ্টহয় যে, এই সাংস্কৃতিক সংঘাত কেবল সামাজিক বা ধর্মীয় নয়, এটি মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, বিশ্বপুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষা এবং আদর্শিক আধিপত্য বিস্তারের এক জটিল প্রক্রিয়া। লোকায়ত সংস্কৃতি, যাযুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনবোধ, সহনশীলতা এবং অসাম্প্রদায়িকতাকে লালন করেছে, তাকেরক্ষা করা আজ জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
১. লোকায়ত দর্শন ও মানবতাবাদ: সহনশীলতার ঐতিহাসিক ভিত্তি-
বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে এখানকার সুফিবাদী, বৈষ্ণববাদী ধর্ম দর্শন এবং বিভিন্ন লোকজ প্রথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই দর্শনগুলো আনুষ্ঠানিক ধর্মের মূল স্রোত থেকে নিজেদের দূরে রেখে এক গভীর মানব ধর্ম দর্শনের চিন্তাভিত্তি স্থাপন করেছে। সুফিবাদ (যেমন লালন,হাসন রাজা, শাহ আব্দুল করিম) এবং বৈষ্ণববাদ (যেমন শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত) প্রচার করেছে প্রেম, সাম্য, এবং দেহ-তত্ত্বের দর্শন, যেখানে জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। এই ভাবধারাগুলো মূলত আনুষ্ঠানিক ধর্মের কঠোরতা ও বিভেদকে প্রত্যাখ্যান করে আন্তজন ও সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলেছিল, বিশেষত গ্রামীণ জনপদে, যেখানে সমাজের শ্রেণিবৈষম্য ছিল প্রকট। সুফিবাদ ও বাউল দর্শনে সহজ মানুষ বা মনের মানুষ এর ধারণাটি মূলতশ্রেণী-বর্ণ-ধর্মের ভেদাভেদহীন এক সাম্যবাদী আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। এই লোকায়ত মানবতাবাদী চেতনা কার্যত ধর্মনিরপেক্ষতার ও গণতন্ত্রের ধৈর্য্য এবং ধর্মনিরেপেক্ষতার বীজ বপন করেছে। এটি মানুষকে শিখিয়েছে—ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়, কিন্তু সমাজের ভিত্তি হলো পারস্পরিক সহনশীলতা ও ভালোবাসা। সুফিবাদীরা কেবল ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন না, তারা ছিলেন সামাজিক দার্শনিক, যাঁরা সমাজে আউটসাইডার হিসেবে বিবেচিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরেছেন। ঐতিহাসিকভাবেই এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলে মিলেমিশে নিজস্ব উৎসব ও প্রথা পালন করেছে, যা এক মিশ্র সংস্কৃতির (Syncretic Culture) জন্ম দিয়েছে। এই লোকজ দর্শনই হচ্ছে বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা, যা যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় উগ্রতাকে সমাজের মূল স্রোতে আসতে দেয়নি। এই সাংস্কৃতিক ভিত্তিই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো আমদানি করা ধারণা নয়, বরং এটি এই মাটির সহজাত সংস্কৃতি ও দর্শনেরই ফসল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্যতম আদর্শিক ভিত্তি।
২. ধর্ম এবং লোকসংস্কৃতির সংঘাত: উগ্র ধর্মবাদের রাজনৈতিক আধিপত্য-
সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে সকল জাতিগোষ্ঠী সময়ের সাথে তাদের লোকজ দর্শনের বিকাশ ঘটিয়েছে। এই লোকজ দর্শন প্রায়শই বিভিন্ন ধর্মের মূল স্রোত থেকে দূরে থেকেছে বা তা প্রতিবাদ করেই হয়েছে। এই কারণেই ধর্ম এবং লোকসংস্কৃতি ঐতিহাসিকভাবে সংঘাতে জড়িয়েছে এবং এই সংঘাতের তীব্রতা বাড়িয়েছে উগ্র ধর্মবাদ। লোকসংস্কৃতি, যেমন যাত্রা, পালাগান, ভাস্কর্য, বাউল গান, পহেলা বৈশাখের উৎসব এগুলো জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ, হাসি-কান্না ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে উদযাপন করে। কিন্তু উগ্র ধর্মবাদ এটিকে বেদাত (ধর্মীয় কুসংস্কার) বা শিরক (একত্ববাদের লঙ্ঘন) আখ্যা দিয়ে এর ওপর আঘাত হেনেছে। বাংলাদেশে এই সংঘাতটি আরও তীব্র হয়েছে ইসলামের নামে ওহাব-সালাফীদের উগ্র আদর্শবাদের আধিপত্য বিস্তারের ফলে। এই আদর্শবাদ একটি রাজনৈতিক ইসলাম হিসেবে সমাজে আসন গেড়েছে। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি হলো গ্রামসির ভাষায়, এক ধরনের কাউন্টার-হিজেমনি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, যেখানে দেশীয় সংস্কৃতিকে বাতিল করে একটি আমদানি করা, কঠোর আরবীয় ধর্মীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই আদর্শিক পরিবর্তন সমাজের বহুত্ববাদ (Pluralism)-কে অস্বীকার করে একটি একমুখী (Monolithic) সমাজ তৈরি করতে চায়। এই রাজনৈতিক ইসলাম কেবল ধর্মীয় পরিশুদ্ধি চায় না, এটি মূলত ক্ষমতা দখল এবং বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার পিছন পিছন হাটছে। এই উগ্র আদর্শের প্রচারকারীরা লোকসংস্কৃতিকে শোষণের বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে ভয় পায়, তাই তারা একে ধ্বংস করতে চাইয়।
৩. রাজনৈতিক ইসলামের বিশ্বায়ন ও ক্ষমতার সমীকরণ-
বাংলাদেশের রাজনীতিতে উগ্র ধর্মবাদের উত্থান স্থানীয় নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি এবং অর্থ প্রবাহ। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইসলামকে এদেশের শাসকগোষ্ঠীর দলগুলি ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করেছে। স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্বল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো, ক্ষমতার দখল নিয়ে অস্থিরতা এবং আদর্শিক স্খলন চরমপন্থী ধর্মীয় শক্তিকে তাদের এজেন্ডা চালানোর সুযোগদিয়েছে। এই শক্তিকে শাসকগোষ্ঠী হয় সরাসরি প্রশ্রয় দিয়েছে, অথবা ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য ব্যবহার করেছে, যা এক অর্থে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উগ্রবাদের বিস্তারকে উৎসাহিত করেছে। এই রাজনীতি ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে চরম জঙ্গী এবং ওহাবী মতবাদী শক্তি এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ পাকিস্তান, তুরস্ক, কাতার, সৌদি আরব-এর মতো দেশগুলোর ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এই শক্তিগুলো ধর্মীয় রাজনীতির পিছনে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক বিনিয়োগ করছে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলো থেকে আসা বিপুল পরিমাণ অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ধর্মীয় প্রচারের আড়ালে ওহাবী আদর্শের প্রচার-প্রসারে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি একটি ট্রান্সন্যাশনাল আদর্শিক নেটওয়ার্ক (Transnational Ideological Network), যা স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধকে ধ্বংস করতে চায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই অঞ্চলে তার কৌশলগত স্বার্থ (যেমন, আঞ্চলিক প্রতিপক্ষের প্রভাব মোকাবিলা) বজায় রাখতে অনেক সময় এই ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর উত্থানকে হয় উপেক্ষা করেছে, অথবা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করেছে, যা উগ্রবাদের বিস্তারকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই প্রক্রিয়াটি অর্থনৈতিক অসমতাকে কাজে লাগিয়ে তরুণদের মধ্যে দ্রুত উগ্র মতাদর্শ ছড়িয়ে দেয়।
৪. প্রতিরোধ ও পাল্টা বয়ান: লোকায়ত সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তি-
বাংলাদেশের প্রবাহমান সংস্কৃতি পারস্পরিক সহনশীলতার ধারায় লালিত। কিন্তু গণবিরোধী শাসকের সেই সহনশীলতা ভেঙেছে বার বার। ক্ষমতা দখলের নেশায় সরকারগুলো যখন জনমুখী নীতি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ দেখেছে, তখনই উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো সেই শূন্যস্থান পূরণ করার সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশে নব উত্থিত মৌলবাদ তার ক্ষমতা দখলের খেলায় ধর্মবাদী শক্তি যে আগ্রাসন পরিচালনা করছে, তা মোকাবিলা করতে হলে একটি সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিরোধের পাল্টা বয়ান তৈরি করা আবশ্যক। এই প্রতিরোধকে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে।
এই প্রতিরোধ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হবে:
১. সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ: বাউল গান, যাত্রা, পালাগান, লোকনৃত্য এবং গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলোকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে লোকজ শিল্পের
সঙ্গে যুক্ত করে উগ্র সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত করতে হবে। এই লোকজ মাধ্যমগুলো হলো সহজ, সরল এবং জনগণের কাছে সহজে পৌঁছানোর মাধ্যম।
২. শিক্ষাব্যবস্থায় লোকায়ত দর্শন: লোকায়ত সংস্কৃতি, সুফিবাদ ও বৈষ্ণববাদের মানবতাবাদী দর্শনকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে তরুণদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা (Critical Thinking) এবং বহুত্ববাদী সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই মানবতাবাদী দর্শনকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৩. রাজনৈতিক অঙ্গীকার: মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষে থাকা সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে অবশ্যই রাজনৈতিক ইসলামের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং দল-মত নির্বিশেষে ধর্মীয় উগ্রতার বিরুদ্ধে
একজোট হতে হবে। এই রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমেই কেবল উগ্রবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎসগুলো বন্ধ করা সম্ভব।
৪. অর্থনৈতিক সাম্য: বামপন্থী রাজনীতির আলোকে, তরুণদের মধ্যে লোকায়ত দর্শনের যে সাম্যবাদী বীজ রয়েছে, তাকে পুঁজি করে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে হবে। এই সংগ্রাম কেবল সাংস্কৃতিক নয়, এটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই। লোকায়ত সংস্কৃতি কেবল ইতিহাস বা বিনোদন নয়, এটি এই অঞ্চলের মানুষের গভীরতম রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রতিরোধের হাতিয়ার। এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করা মানেই ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং মানবতাবাদী বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে রক্ষা করা। উগ্র ধার্মান্ধদের আঘাতকে প্রতিহত করতে হলে, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে লোকায়ত সংস্কৃতির মানবতাবাদী মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।
লেখক: ‘৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের ছাত্রনেতা, তৎকালীন বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক