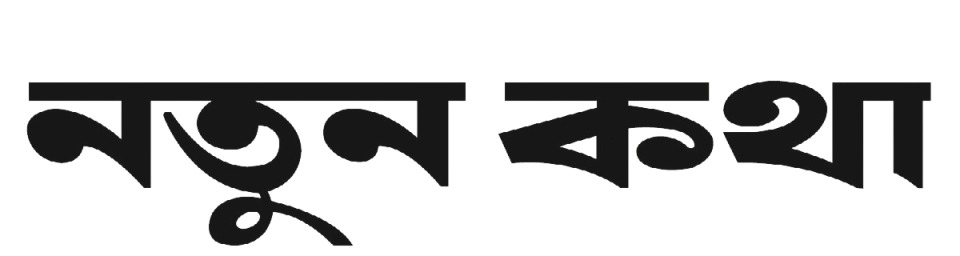নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাকাপোক্ত করতে রাজধানী বেইজিংয়ে জড়ো হয়েছেন চীনের শীর্ষ নেতারা। সেখানে তারা ২০২৬-২০৩০ সালের কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন। বিশেষ করে আগামী পাঁচ বছর অর্থনৈতিকভাবে চীন নিজেদের কোন কোন লক্ষ্য পূরণ করতে চায় তার রূপরেখা এবং কর্মপদ্ধতি ঠিক হবে এই বৈঠকে। চীনে প্রতিবছরই এমন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বেইজিংয়ে সপ্তাহব্যাপী চলে এসব বৈঠক। সেখান থেকে তারা পরবর্তী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন এবং লক্ষ্য পূরণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করেন। কাগজে কলমে চীনের এই পদ্ধতি সাদামাটা মনে হলেও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। চীনের এসব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিশ্বের অর্থনৈতিক গতিপথ বদলে দেয়ার নজিরও রয়েছে। এ ছাড়া এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের ফেলো নীল থমাস বলেন, পশ্চিমা নীতি নির্বাচনী চক্রে পরিচালিত হয়। আর চীনের নীতিনির্ধারণ চলে পরিকল্পনা চক্রে। চীনের এসব পরিকল্পনা দেশটির লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা দেয়। বিশেষ করে দেশটির নেতৃত্বের অভিমুখ কোন পথে তা জানা যায়। অতীতের তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কীভাবে বিশ্ব অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে, তার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিবিসি।
সেখানে বলা হয়, চীনের উত্থান-পর্ব হিসেবে ধরা হয় ১৯৮১-৮৪ সালকে। কমিউনিস্ট নেতা মাও সেতুংয়ের বিধ্বংসী শাসন ও সোভিয়েত-শৈলীর কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি যখন দেশের সমৃদ্ধি আনতে ব্যর্থ হয়, তখন নতুন নেতা দেং জিয়াও পিং মুক্তবাজার অর্থনীতির কিছু উপাদানকে গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে শুরু হওয়া ওই পরিকল্পনায় সংস্কার ও উন্মুক্তকরণকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি এবং তাতে বিপুল বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার মধ্যদিয়ে চীনের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিত হয়।
এর বৈশ্বিক প্রভাব ছিল ব্যাপক। একবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা দেশগুলোর উৎপাদন খাতের বহু কাজ চীনের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। যা ইতিহাসে চায়না শক নামে পরিচিত। এর পেছনে রয়েছে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক শিল্পাঞ্চলে জনপ্রিয়তাবাদী দলগুলোর উত্থান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ এবং শুল্কনীতির প্রধান লক্ষ্য চীন। এর মাধ্যমে চীনের দখলে চলে যাওয়া হারানো সেই আমেরিকান শিল্প ফিরিয়ে আনতে চান ট্রাম্প।
২০০১ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) যোগ দিয়ে চীন নিজেদের অবস্থান পাকা করেছে। এরপরই কম মজুরি আর সস্তা উৎপাদনের গণ্ডি পেরিয়ে এবার নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে উচ্চ-প্রযুক্তিগত পণ্য ও পরিষেবা তৈরির উদ্ভাবনী ক্ষমতা আয়ত্ত করার পরিকল্পনা করে চীন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে চীন কৌশলগত উদীয়মান শিল্পের ওপর মনোযোগ দেয়। যার মধ্যে প্রধান ছিল সবুজ প্রযুক্তি। যেমন ইলেকট্রিক যান এবং সৌর প্যানেল। জলবায়ু পরিবর্তন যখন পশ্চিমা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো, চীন তখন এই শিল্পগুলোতে অভূতপূর্ব সম্পদ বিনিয়োগ শুরু করে। এর ফলস্বরূপ, আজ চীন কেবল নবায়নযোগ্য শক্তি এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্ষেত্রে সবার উপরে নয় বরং এই প্রযুক্তি ও সেমিকন্ডাক্টর (চিপ) তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বিরল খনিজ সরবরাহেও প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে বেইজিং। কৌশলগত এই সম্পদগুলোর ওপর চীনের নিয়ন্ত্রণ বিশ্ব জুড়ে তাদের ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। নীল থমাসের মতে, অর্থনীতি ও প্রযুক্তিতে চীনের এই আত্মনির্ভরশীলতার আকাক্সক্ষা কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শের মূলে প্রোথিত।
বর্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শি জিনপিং প্রবর্তিত ‘উচ্চমানের উন্নয়ন’ স্লোগানটি প্রযুক্তি খাতে আমেরিকান আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার দিকে মনোনিবেশ করেছে। টিকটক, হুয়াওয়ে এবং ডিপসিক-এর মতো ঘরোয়া সাফল্যের গল্পগুলো চীনের এই প্রযুক্তিগত উত্থানের প্রমাণ। তবে পশ্চিমাদের এই প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রাকে তাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ফলে চীনা প্রযুক্তির ওপর বিশ্ব জুড়ে নিষেধাজ্ঞা বা নিষেধাজ্ঞার প্রচেষ্টা কূটনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। বর্তমান পরিকল্পনা বৈঠক চলাকালীন যুক্তরাষ্ট্র চীনের কাছে উন্নত সেমিকন্ডাক্টর বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে চীন এখন নতুন স্লোগানের দিকে ঝুঁকছে। যার প্রধান লক্ষ্য হলো প্রযুক্তি খাতে স্বনির্ভর হওয়া। বিশেষ করে চিপ তৈরি, কম্পিউটিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর মতো শীর্ষস্থানীয় উদ্ভাবনী ক্ষেত্রগুলোতে পশ্চিমা প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করাই পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে বলে মনে করা হচ্ছে। নীল থমাসের বলছেন, জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত স্বাধীনতা এখন চীনের অর্থনৈতিক নীতির সংজ্ঞায়িত মিশন। আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিশ্বকে কোন নতুন পথে নিয়ে যায় সেটাই এখন দেখার বিষয় বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা।