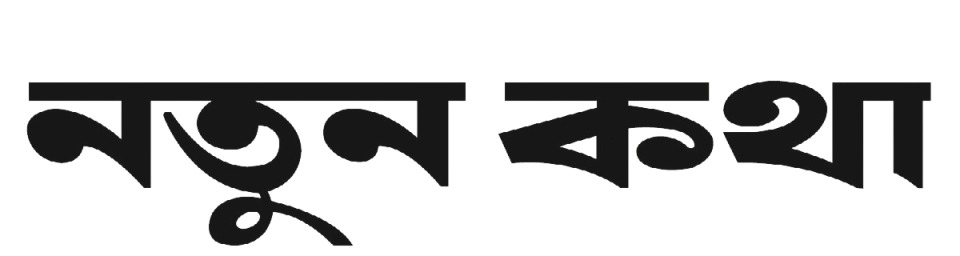।। শরীফ শমশির ।।
“আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর।”-বঙ্গবন্ধু (আত্মজীবনী, পৃ: ২৩৪)।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)-এর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে ১৯৩৬-৩৭ সালের দিকে, বিশেষ করে মিশন স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তাঁর সঙ্গে যখন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। তার আগে নানা সামাজিক কর্মকা-ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি সোহরাওয়ার্দীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় ১৯৩৯ সালে তৎকালীন মুসলিম ছাত্রলীগে যুক্ত হন। একই সঙ্গে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিতেও প্রবেশ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে বেকার হোস্টেলের আবাসিক ছাত্র থাকাকালীন ছাত্রনেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।
১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে লাহোর প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হলে বঙ্গবন্ধু তাতে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি দেখলেন মুসলিম লীগের নেতৃত্ব জমিদার, জোতদার ও খান বাহাদুরদের দখলে; একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে অর্থাৎ জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সংগ্রামে নিয়োজিত হন। এভাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর রাজনৈতিক গুরুতে পরিণত হন এবং তিনি গণতন্ত্রের ধারাকে রাজনীতির আদর্শ হিসেবে বেছে নেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তখন রাজনীতিতে অস্তগামী। বাংলাদেশে প্রজাদের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে কয়েকদিনের কোয়ালিশন সরকার গঠন করায় তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ব্যাপক অপপ্রচার শুরু করে। এ কারণে মুসলিম তরুণদের মধ্যে তিনি কিছুটা জনপ্রিয়তা হারান। তাই এ কে ফজলুল হকের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে গণতান্ত্রিক রাজনীতিকেই মূলমন্ত্র হিসেবে নেন। সোহরাওয়ার্দীর পরে আবুল হাসিম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলে তিনি তাঁর সাথেও কাজ করেন। আবুল হাসিমকে তখন বলা হতো বামপন্থী মুসলিম লীগ নেতা। ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ চালু করেছিলেন আবুল হাসিম। সেখানে তিনি বলতেন, পাকিস্তান দাবি হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয় বরং হিন্দু-মুসলমানকে মিলানো এবং দুইভাই যাতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে তারই জন্য। এই সময় বঙ্গবন্ধু আবুল হাসিমের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসভায় যোগদান করেছেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, “আমি ছিলাম শহীদ সাহেবের ভক্ত। হাসিম সাহেব শহীদ সাহেবের ভক্ত ছিলেন বলে আমিও তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, তাঁর হুকুম মানতাম।” (আত্মজীবনী, পৃ: ২৪)।
বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন জবানীতে দেখা যায় ভারতবিভাগপূর্ব কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবে তাঁর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতার চেতনা বিকশিত হয়। এছাড়া, তিনি ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্তদের জন্য লঙ্গরখানা পরিচালনা করেছেন, ’৪৬-এর দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমানকে রক্ষা করতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে জনদরদি ছাত্রনেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগ সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্রদের অধিকার, কর্মচারীদের দাবির পক্ষে আন্দোলনসহ ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং কারাবন্দি হন।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর বঙ্গবন্ধুসহ পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদগণ প্রত্যক্ষ করলেন পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন হলেও সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু ১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করে অল্প দিনের মধ্যেই জনগণকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে এসেছে। চীন বিপ্লবের প্রভাব পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনেও ঢেউ তোলেছিল। আদর্শিক না হলেও বঙ্গবন্ধুর চেতনায় এ বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। একটা কথা এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়েছিল এবং অনেক দেশ উপনিবেশের জোয়াল ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতা এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আগ্রাসী যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে সদ্য স্বাধীন দেশগুলো একজোট হয়ে গড়ে তুলেছিল জোটনিরপেক্ষ এবং বিশ্ব শান্তি আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিকভাবে এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হন। যদিও এসময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানকে মার্কিনী জোটে বিশেষ করে সিয়াটো ও সেন্টু চুক্তিতে আবদ্ধ করেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জোটনিরপেক্ষ ও শান্তি আন্দোলনে আস্থা রাখলেন। সোহরাওয়ার্দীর বিখ্যাত তত্ত্ব ছিল শূন্য + শূন্য = শূন্য, অর্থাৎ পাকিস্তানকে এমন একটি জোটে থাকতে হবে যাতে পাকিস্তানের আর্থিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক গুরুর সঙ্গে নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক নীতির বিষয়ে প্রকাশ্যে দ্বিমত না করলেও পূর্ব বাংলার জনগণের সার্বিক কল্যাণ তিনি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সাথে সামরিক চুক্তিতে দেখেননি; দেখেছিলেন শান্তির মধ্যে। শান্তিকালীন জাতীয় উন্নয়ন জনগণের জন্য অধিক উপকারি বলে বঙ্গবন্ধু মনে করতেন। তিনি লিখেছিলেন, “আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর।” (আত্মজীবনী, পৃ: ২৩৪)। তিনি আরো লিখেছেন, “নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা। যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে যারা আবদ্ধ ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদের সর্বস্ব লুট করেছে- তাদের প্রয়োজন নিজের দেশকে গড়া ও জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। বিশ্বশান্তির জন্য জনমত সৃষ্টি করা তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।” (আত্মজীবনী, পৃ: ২৩৪)। ফলে ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি বঙ্গবন্ধুর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন একটি সমাজ গঠন করা যায়-এরকম একটি ধারণাও তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করে। তবে সমাজতন্ত্রের ধারণাটি তিনি বিনা পরখে মানতে রাজি ছিলেন না। তাই, যখন চীন ভ্রমণের সুযোগ আসলো তখন তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণসহ তা পরখ করেছিলেন।
১৯৫২ সালের ২-১২ই অক্টোবর চীনের পিকিং এ অনুষ্ঠিত এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নয়াচীন সফর করেন। ১৯৫৪ সালে কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে তিনি চীন সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেন “আমার দেখা নয়াচীন” এটি বাংলা একাডেমি ২০২০ সালে পুস্তক আকারে প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু চীন সফরের এই অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তেও বিবৃত করেছেন। এতে বোঝা যায় যে চীন সফরকে বঙ্গবন্ধু খুই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন। সার্বিকভাবে বঙ্গবন্ধুর চীন সফরের এই অভিজ্ঞতা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা গঠনেও সহায়তা করেছে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন।
১৯৫৭ সালেও মন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু চীন সফর করেছেন কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কিছু লিখে যান নি, ফলে ১৯৫২ সালের ভ্রমণের লিখিত বইটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পাশাপাশি সাধারণ পাঠককেও কৌতূহলী করেছে। কারণ এ রচনায় তিনি সদ্য বিপ্লবোত্তর গণচীনের জীবনযাত্রা ও শাসন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণী মন নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন।
বিপ্লবের (১৯৪৯) মাত্র তিন বছর পর চীনের সমাজে এবং শাসনে বেশকিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল যার খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পূর্ব বাংলায়ও এসে পৌঁছাত। এসব খবর অন্যান্যের মতো বঙ্গবন্ধুকেও ভাবাত। বঙ্গবন্ধুর এই ভাবনা ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায়। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পূর্ব বাংলার মুসলমানের সম্পৃক্ততা শুধু গভীর ধর্মীয় ভাবাবেগের বিষয় ছিল না; ছিল নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আকাক্সক্ষাও। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদগণ যখন অনুধাবন করলেন পশ্চিম পাকিস্তান পাকিস্তানের সব কিছুর কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পূর্ব বাংলা অবহেলিত থেকে যাচ্ছে তখন তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। এছাড়া, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলার দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বহু লোক না খেয়ে মারা যায় এবং কৃষকরা তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে হয়রানির শিকার হয়েছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারেও পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব ধীরে ধীরে কমে আসছিল এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পূর্ববঙ্গের তরুণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি চাকরিসহ ব্যাবসাবাণিজ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে।
এসব পর্যবেক্ষণ করে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনায়ও পরিবর্তন আসে। তাই নতুন রাষ্ট্র কীভাবে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করছে তা দেখার আকাঙ্খা থেকে নয়াচীন ভ্রমণের আগ্রহ জন্মে তাঁর মনে।
বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, “১৯৫২ সালে জেল থেকে বের হলাম, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর। জেলে থাকতে ভাবতাম আর মাঝে মাঝে মওলানা ভাসানী সাহেবও বলতেন, ‘যদি সুযোগ পাও একবার চীন দেশে যেও।’ অল্প দিনের মধ্যে তারা কত উন্নতি করেছে। চীন দেশের খবর আমাদের দেশে বেশি আসে না এবং আসতে দেওয়াও হয় না। তবুও যতটুকু পেতাম তাতেই মনে হতো যদি দেখতে পেতাম কেমন করে তারা দেশকে গড়েছে।” (নয়াচীন, পৃ: ১৯)।
ফলে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন পাকিস্তান শান্তি কমিটি পিকিং এ অনুষ্ঠিতব্য শান্তি সম্মেলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তিনি পূর্ববাংলা থেকে অন্যান্যের সঙ্গে সেই প্রতিনিধি দলের সঙ্গী হন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন কেন তিনি শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকটা কৈফিয়তের ভঙ্গিতেই তিনি লিখেছেন, “কথাটা সত্য যে, আমরা কমিউনিস্ট না। তথাপি দুনিয়ায় আজ যারাই শান্তি চায় তাদের শান্তি সম্মেলনে আমরা যোগদান করতে রাজি। রাশিয়া হউক, আমেরিকা হউক, ব্রিটেন হউক, চীন হউক যে-ই শান্তির জন্য সংগ্রাম করবে তাদের সাথে আমরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে রাজি আছি, ‘আমরা শান্তি চাই’।” (নয়াচীন, পৃ: ১৯)।
শান্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর এই চেতনা যুদ্ধের ভয়াবহতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। তিনি দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং কৃষকের দুর্দশা। তিনি লিখেছেন, “যুদ্ধে দুনিয়ার যে ক্ষতি হয় তা আমরা জানি এবং উপলব্ধি করতে পারি; বিশেষ করে আমার দেশে-যে দেশকে পরের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, কাঁচামাল চালান দিতে হয়। যে দেশের মানুষ না খেয়ে মরে, সামান্য দরকারি জিনিস যোগাড় করতে যাদের জীবন অতিষ্ট হয়ে ওঠে, সে দেশে যুদ্ধে যে কতখানি ক্ষতি হয় তা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা মনে করলেই বুঝতে পারবেন। কোথায় ইংরেজ যুদ্ধ করছে, আর তার জন্য আমার দেশের লক্ষ লোক শৃগাল, কুকুরের মতো না খেয়ে মরেছে। তবুও আপনারা বলবেন, আজ তো স্বাধীন হয়েছি। কথা সত্য, ‘পাকিস্তান’ নামটা পেয়েছি; আর কতটুকু স্বাধীন হয়েছি আপনারা নিজের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন।” (নয়াচীন, পৃ: ১৯-২০)।
বঙ্গবন্ধুর এই যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তৈরি হয় দেশের মানুষের মঙ্গলের কথা ভেবে। শান্তিকেও তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন একারণে। তিনি লিখেছেন, “… পাকিস্তান গরীব দেশ, যুদ্ধ চাইতে পারে না। যুদ্ধ হলে পাকিস্তানের জনগণের সকলের চেয়ে বেশি কষ্ট হবে এই জন্য। তাদের পাট, চা, তুলা অন্যান্য জিনিস বিদেশে বিক্রি না করলে দেশের জনগণের কষ্টের সীমা থাকবে না। দুর্ভিক্ষ মহামারি সমস্ত দেশকে গ্রাস করবে। তাই মানুষের মঙ্গলের জন্য, পাকিস্তানের স্বার্থের জন্যÑযুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।” (নয়াচীন, পৃ: ২০)।
বঙ্গবন্ধুর এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বোঝা যায় শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য পিকিং যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর গভীর রাজনৈতিক উপলব্ধিপ্রসূত। এই উপলব্ধির কেন্দ্রে রয়েছে দেশের সাধারণ জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়ন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কোনো দেশ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেই স্বাধীন হয় না, যতক্ষণ না সে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি বা উন্নয়ন না ঘটে।
বিশ্বশান্তির জন্য একটি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে বঙ্গবন্ধুর চীন সফর হলেও ‘আমার দেখা নয়াচীন’ গ্রন্থটি স্রেফ সফরের দিনলিপি নয়, বরং এটি হলো বৈশ্বিক রাজনৈতিক সমাবেশে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা, একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর পর্যবেক্ষণ এবং নিজ দেশের জন্য প্রযোজ্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক করণীয় নির্ধারণ করাও।
অন্যদিকে এই সফরের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করতে বঙ্গবন্ধু বিশ্বরাজনীতির বিশ্লেষণসহ জনগণের সার্বিক মুক্তির পথের দিশাও খোঁজার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে মানুষের মুক্তির রাজনৈতিক দর্শনও পর্যালোচনা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় তিনি ফিলোসফি বুঝতে চেষ্টা করেন নি; তিনি চেষ্টা করেছেন বাস্তবে আদর্শ কীভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে।
ফলে বঙ্গবন্ধু ‘আমার দেখা নয়াচীন’ গ্রন্থের শুরু থেকেই একটি বিশ্লেষণী ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে যা কিছু দেখেছেন তার সবটুকু লেখার চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা দিয়ে লেখাটি শেষ করেছেন।
‘আমার দেখা নয়াচীন’ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু পাসপোর্ট সংগ্রহ, রেঙ্গুন ও হংকং অবস্থানসহ চীন সফরের প্রত্যেকটি স্থানের বর্ণনা যেমন দিয়েছেন তেমনি দিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসাবশত ভ্রমণ, সাক্ষাতকার ও অভিজ্ঞতার।
বঙ্গবন্ধুর এই সফরের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ: (ক) তেজগাঁ অ্যারোড্রাম থেকে রেঙ্গুন। রেঙ্গুনে অর্ধবেলা ও একরাত অবস্থান। (খ) তারপর ব্যাংকক হয়ে হংকং। (গ) পরের দিন হংকং থেকে চীনের ক্যান্টন। (ঘ) এরপর বিমানে পিকিং শহরে। এগারো দিন সম্মেলন চলে। (ঙ) এরপর নানকিং, সাংহাই হয়ে পুনরায় হংকং হয়ে দেশে ফিরে আসা। এই সমগ্র সফর ছিল পঁচিশ দিনের। এই পঁচিশ দিনে তিনি ট্রেনে, বিমানে, রিকশায় যখন যেখানে যেভাবে ভ্রমণ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। যাদের সঙ্গে কথোপকথন করেছেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন দেশের নেতাদের বর্ণনা যেমন দিয়েছেন তেমনি তিনি প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের বক্তব্যও তুলে ধরেছেন। পরিশেষে একটি সুগভীর তুলনামূলক ও তর্কমূলক পর্যবেক্ষণও দিয়েছেন যাতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।
রেঙ্গুন ও হংকং এ বঙ্গবন্ধুর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দেখা গেছে। রেঙ্গুনে তখন সরকার এবং কমিউনিস্ট বিদ্রোহী বিশেষ করে কারেনদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল। এতে করে রেঙ্গুনের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বেশ অবনতি হয়েছিল। রেঙ্গুনে বঙ্গবন্ধু ও সফরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গদান করেন আতাউর রহমান খান সাহেবের আত্মীয়ের ছেলে আজমল খাঁ। তিনি রেঙ্গুনে ব্যবসা করতেন। এই সফরে বঙ্গবন্ধু খেয়াল করলেন বার্মায় নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ঢাকার একজন মিষ্টিভাষী হলেও বেশ আয়েশি জীবনযাপন করেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, “রাষ্ট্রদূত অনেক জাঁকজমকের সাথেই থাকেন, বিরাট অফিস ও বহু কর্মচারি তাঁকে সাহায্য করে। দেখে মনে হলো, যাদের টাকা দিয়া এত জাঁকজমক তাদের অবস্থা চিন্তা করলেই ভালো হতো। তাদের ভাতও নাই, কাপড়ও নাই, থাকবার মতো জায়গাও নাই। তাদের কেউ না খেয়ে, রাস্তায় ঘোরে।” (নয়াচীন, পৃ: ২৩)।
হংকং-এ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের কয়েকজন হিন্দু দোকানদারের সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করেন। সেখানেও তিনি দেশের ভালো দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কারণ বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, “দেশের ভেতরে আমাদের সরকারের অন্যায়-অত্যাচার সম্বন্ধে বললেও বিদেশে বলার পক্ষপাতি আমরা নই কারণ এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলে মনে করি।” (নয়াচীন, পৃ: ২৬)
শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল। একটি হলো ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাশ্মীর প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব গ্রহণ। প্রস্তাবের সারাংশ ছিল গণভোটের দ্বারা ঠিক হবে কাশ্মীর কোন দেশে যোগদান করতে চায়। দ্বিতীয় হলো বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া। বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, “বাংলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় বক্তৃতা করাই উচিত। কারণ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু কিছু জানে। মানিক ভাই, আতাউর রহমান খান ও ইলিয়াস বক্তৃতাটা ঠিক করে দিয়েছিল। দুনিয়ার সকল দেশের লোকই যার যার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করে। শুধু আমরাই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করে নিজেদের গর্বিত মনে করি।” (নয়াচীন, পৃ: ৪৩)। মাতৃভাষা বাংলাকে বিশ্ব দরবারে উচ্চারণ করার এই মনোভাব বঙ্গবন্ধুর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।
বঙ্গবন্ধু চীনকে দেখতে এবং বুঝতে চেয়েছিলেন। চীনের জনগণের প্রকৃত অবস্থা তিনি চীনের সরকারি ব্যবস্থাপনার বাইরে গিয়েও বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। কনফারেন্সের মধ্যে তাঁরা চীনের বিখ্যাত জায়গা, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, মসজিদ, শ্রমিকের অবস্থা ও কৃষি ব্যবস্থা দেখতে যেতেন। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু একা প্রায়ই একটা রিকসা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।
বঙ্গবন্ধু যেসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন সেগুলোর অন্যতম হলো শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন, বেকার সমস্যা দূর করা, ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং উন্নয়মূলক কর্মকা- ইত্যাদি।
বঙ্গবন্ধু দেখেছেন শুধু আইন করে নয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করে চীনে ভিক্ষা ও গণিকাবৃত্তি বন্ধ করা হয়েছে। জনগণের সহায়তায় ডাকাতি ও ঘুষ খাওয়া বন্ধ করা হয়েছে। আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ না হলেও জনগণের মধ্যে শান্তি এবং স্বস্তি ফিরে এসেছিল। রাষ্ট্রীয় ডাকে জনগণ স্বেচ্ছাশ্রমে সেচ, বাঁধসহ নানা বড়ো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। জনগণ পঞ্চায়েত নির্বাচনসহ স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বারবার নিজ দেশের দুর্দশার কথাও বিস্তারিত উল্লেখ করেন। এছাড়া যে সব নীতিমালা মানুষের জীবন ও মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয় সে সবেরও তিনি উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধু চীনে আরো কয়েকটি বিষয় নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের অন্যতম হলো; কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি, কুঠির শিল্পের প্রসার, ভূমি সংস্কার করে বেকারত্বের হার কমিয়ে আনাসহ নারীদের কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হওয়া। বঙ্গবন্ধু চীনে ধর্মীয় পরিস্থিতিসহ মানুষের মৌলিক অধিকার কেমন আছে-তাও পর্যবেক্ষণ করেছেন।
বঙ্গবন্ধু আফসোস করে লিখেছেন নিজের দেশে সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এটি সমাজে একটি ব্যাধি হিসেবে বিরাজ করছে। দেশে ঘুষ, দুর্নীতি ও চোরাকারবারির বিরুদ্ধে কঠোর কোনো আইনও নেই এবং যা আছে তার কোনো প্রয়োগও নেই। তাই চীনে দুর্নীতি, চোরাকারবারি ও আফিম খাওয়া বন্ধ হয়েছে দেখে বঙ্গবন্ধু আনন্দিত হয়েছিলেন।
বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, “নয়াচীন ঘুরে এসে আমার এই মনে হয়েছে যে, জাতির আমূল পরিবর্তন না হলে দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা কষ্টকর।” (নয়াচীন, পৃ: ১০৭)।
চীনে স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার পরিবেশ আছে কি না তা ভ্রমণের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি সম্মেলনে চীনা মুসলিম প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েছেন এবং খাবারদাবার পরিবেশনের সময় মুসলমানদের জন্য উপযোগী খাবার আছে কি না তাও খেয়াল করেছেন।
সব বিষয় পর্যবেক্ষণ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, “আমাদের দেশে প্রোপাগান্ডা হয়েছে, নয়াচীনে ধর্ম-কর্ম করতে দেওয়া হয় না। এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। আর যদি আমি নয়াচীনে দেখতাম ধর্ম পালন করতে দেওয়া হয় না, তবে সমস্ত দুনিয়ায় এর বিরুদ্ধে আমি প্রোপাগান্ডা করতাম। কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে ধর্মে বিশ্বাসী। এবং নিজে একজন মুলমান বলে গর্ব অনুভব করি।” (নয়াচীন, পৃ: ১১৩)।
বঙ্গবন্ধু আরো উল্লেখ করেছেন চীনে ধর্ম নিয়ে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করার সুযোগ নেই এবং স্থানীয় ইমামরা সরকার এবং ‘অল চায়না ইসলামিক কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন’ এর আর্থিক সহায়তা পায়। বঙ্গবন্ধু আরো লিখেছেন, “নয়াচীনে আজ আর কেহ রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে যার ইচ্ছা ধর্মকর্ম করতে পারে, কেহ তাকে বাধা দিতে পারবে না। আর কেহ ধর্ম পালন না করলেও কেহ জোর করে করাতে পারবে না। দুইটাই নয়াচীনে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। (নয়াচীন, পৃ: ১১৫)।
বঙ্গবন্ধু আরো মন্তব্য করেন এই বলে যে, “নয়াচীন সকলকেই মানুষ হিসাবে বিচার করে; কে কোন ধর্মের তা দিয়ে বিচার হয় না। তাই নয়াচীন সরকার সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে কোনো সরকার এত ভালো কাজ করতে পারে নাই। যারা নয়াচীনে গেছে তাহারাই এদের প্রশংসা করেছে, শুধু আমি একা হতভাগ্য মুগ্ধ হই নাই।” (নয়াচীন, পৃ: ১১৫)।
চীনে নারীদের অগ্রগতির একটি স্পষ্ট চিত্রও বঙ্গবন্ধুর রচনায় পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু নিজ দেশের মেয়েদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে চীনের মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ‘পুরুষ শ্রেষ্ঠ আর স্ত্রী জাতি নিকৃষ্ট’ এই পুরনো প্রথা অনেক দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে, তাহা আর নয়াচীনে নাই। আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আজ নয়াচীনে সমস্ত চাকরিতে মেয়েরা ঢুকে পড়েছে। পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছে। প্রমাণ করে দিতেছে পুরুষ ও মেয়েদের খোদা সমান শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছে।” (নয়াচীন, পৃ: ৯৯)। নতুন বিবাহ প্রথার কারণে বঙ্গবন্ধুর ভাষায় “নয়াচীনে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার কায়েম হওয়াতে আজ আর পুরুষ জাতি অন্যায় ব্যবহার করতে পারে না নারী জাতির ওপর।” (ঐ)
তবে অবিবাহিত মেয়েদের সন্তানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়াটা বঙ্গবন্ধুর ভালো লাগেনি। তিনি লিখেছেন, “নয়াচীন সরকার যে মেয়েদের অবিবাহিতকালে ছেলেমেয়ে হয় তাদের কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করে নাই। অন্যপক্ষে, যদি কেউ তাদের হিংসা বা ঘৃণা করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আমি এটা স্বীকার করি যে, ছেলেমেয়েদের কোনো দোষ নাই। তারা নিরাপরাধ, তাদের যদি কেউ হিংসা বা ঘৃণা করে তবে তাতে যথেষ্ট অন্যায় হবে এবং তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু যে মেয়েদের অবিবাহিতকালে ছেলেমেয়ে হয়, তাদের কোনোরকম শাস্তির ব্যবস্থা না হলে ভবিষ্যতে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে কি না না সেটা ভাববার কথা। যদিও নয়াচীনের অনেকে বলেছে তাতে উন্নতি হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খলতা কমে গেছে। …আমার এখানে মতামত দেওয়া উচিত হবে না। কারণ আমি এদের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারি নাই। তবে প্রথাটা আমার ভালো লাগে নাই। ফলাফলের অপেক্ষায় রইলাম।” (নয়াচীন, পৃ: ১০১)।
চীনের রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, “নয়াচীনে কম্যুনিস্ট নীতি বলে কোনো নীতি দেখলাম না। দেশের ও জনগণের যাতে মঙ্গল হয়, তাই তাদের কাম্য এবং সেই কাজটি তারা করে।” (নয়াচীন, পৃ: ১১৬)। তিনি আরো লিখেছেন, “একথা সত্য যে, তারা কম্যুনিস্ট নীতিতে বিশ্বাসী; তবে, সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে তাদের যথেষ্ট তফাত আছে। রুশ বিপ্লবের পরে সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টি অনেক নতুন পথ অবলম্বন করে ভুল করেছে, পরে আবার তার সংশোধন করেছে। রাশিয়ায় যে ভুল হয়েছে সে ভুল নয়াচীন আজ আর করছে না।” (নয়াচীন, পৃ: ১১৬)। বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট দেশের শাসনব্যবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা করে লিখেছেন, “যে যে দেশে ফ্যাসিস্ট সরকার আর কমিউনিস্ট সরকার কায়েম, সেখানে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক আদর্শকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। আবার অনেক দেশে গণতন্ত্র কায়েম করতে দেয় না সে দেশের সরকার।” (নয়াচীন, পৃ: ১১৬)। এই তুলনামূলক আলোচনায় বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার এবং একদলীয় শাসনে ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধু নয়াচীনের শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী রাজনৈতিক দল বা আদর্শকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে সুযোগ না দেওয়ার বিষয়টির সমালোচনা করেছেন। তিনি পরিশেষে লিখেছেন, “নয়াচীনের অনেক কিছুই আমার ভালো লেগেছিল একথা সত্য। কিন্তু নয়াচীন সরকার কম্যুনিস্ট মতবাদ ছাড়া অন্য কোনো মতবাদের লোককে রাজনীতি করতে দেয় না।” (নয়াচীন, পৃ: ১১৮)।
নয়াচীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে বিতর্কমূলকভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং নিজে দেশের শক্তি ও সীমাবদ্ধতাও তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধু চীন ভ্রমণে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ভাবনাকে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি উপলব্ধী করেছেন যে, সমাজতন্ত্র মানুষকে শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত করে। শিশুদের ভবিষ্যত অবারিত করে দেয়, ভিক্ষাবৃদ্ধি বন্ধ করে, নারীদের মর্যাদাপূর্ণ অধিকার দেয়, বেকারের কর্মসংস্থান করে, ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করে এবং সমাজের সকলের উন্নয়ন নিশ্চিত করে। তাই সার্বিক পর্যালোচনা করে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর নিকট সমাজতন্ত্র মানে ছিল শোষণমুক্তি এবং বৈষম্যহীন একটি সমাজ এবং একইসঙ্গে একটি অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক শাসন। একদলীয় শাসন বা গণতান্ত্রিক শাসন-যে কোনো শাসনে বিরোধী মতামত প্রকাশের সুযোগ না থাকলে তা অনুমোদনযোগ্য নয় বলে বঙ্গবন্ধু মনে করতেন। তিনি লিখেছেন, “আমার মতে, ভাত-কাপড় পাবার ও আদায় করে নেবার অধিকার মানুষের থাকবে, সাথে সাথে নিজের মতবাদ প্রকাশ করার অধিকারও মানুষের থাকা চাই। তা না হলে মানুষের জীবন বোধ হয় পাথরের মতো শুষ্ক হয়ে যায়।” (নয়াচীন, পৃ: ১১৯)।
বঙ্গবন্ধুর চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করতে সহায়তা করেছিল। ফলে ১৯৬৭ সালে আওয়ামী লীগের ম্যানোফেস্টোতে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রও সন্নিবেশিত হয়েছিল। নয়া উদারতাবাদের এই যুগে যেখানে দুনিয়াব্যাপি বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে এবং নানাভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নানা মিথ্যা অপবাদে পারমানবিক যুদ্ধের হুমকি জারি রেখেছে সেখানে বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র এবং বিশ্বশান্তির ধারণা নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেছে।
বঙ্গবন্ধুর ‘আমার দেখা নয়াচীন’ একদিকে যেমন বঞ্চিত-লাঞ্চিত মানুষের মুক্তির অন্বেষায় রাজনৈতিক মতবাদের দলিল তেমনি এই বইকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার দর্পনও বলা চলে। বাংলা সাহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাশিয়ার পত্র’ যেমন চিন্তা উদ্রেককারী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়, তেমনি আমি আশা করি বঙ্গবন্ধু লিখিত ‘আমার দেখা নয়াচীন’ও একটি মহৎ রাজনৈতিক সাহিত্য হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করবে।
লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক।